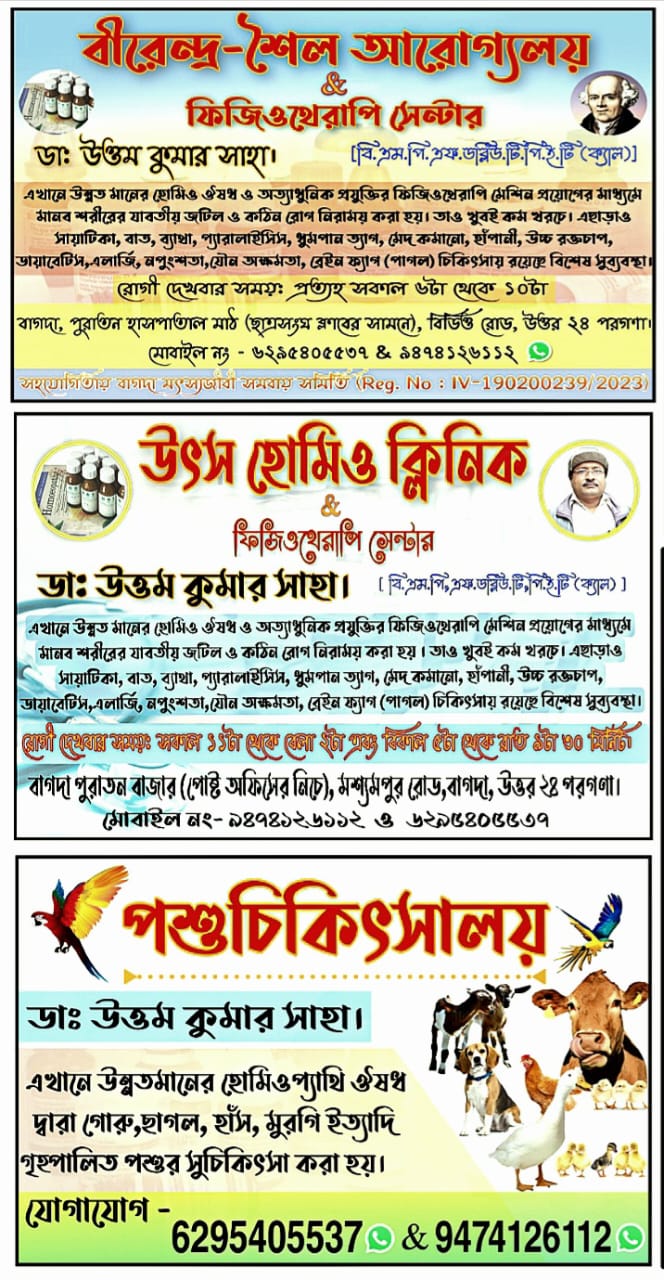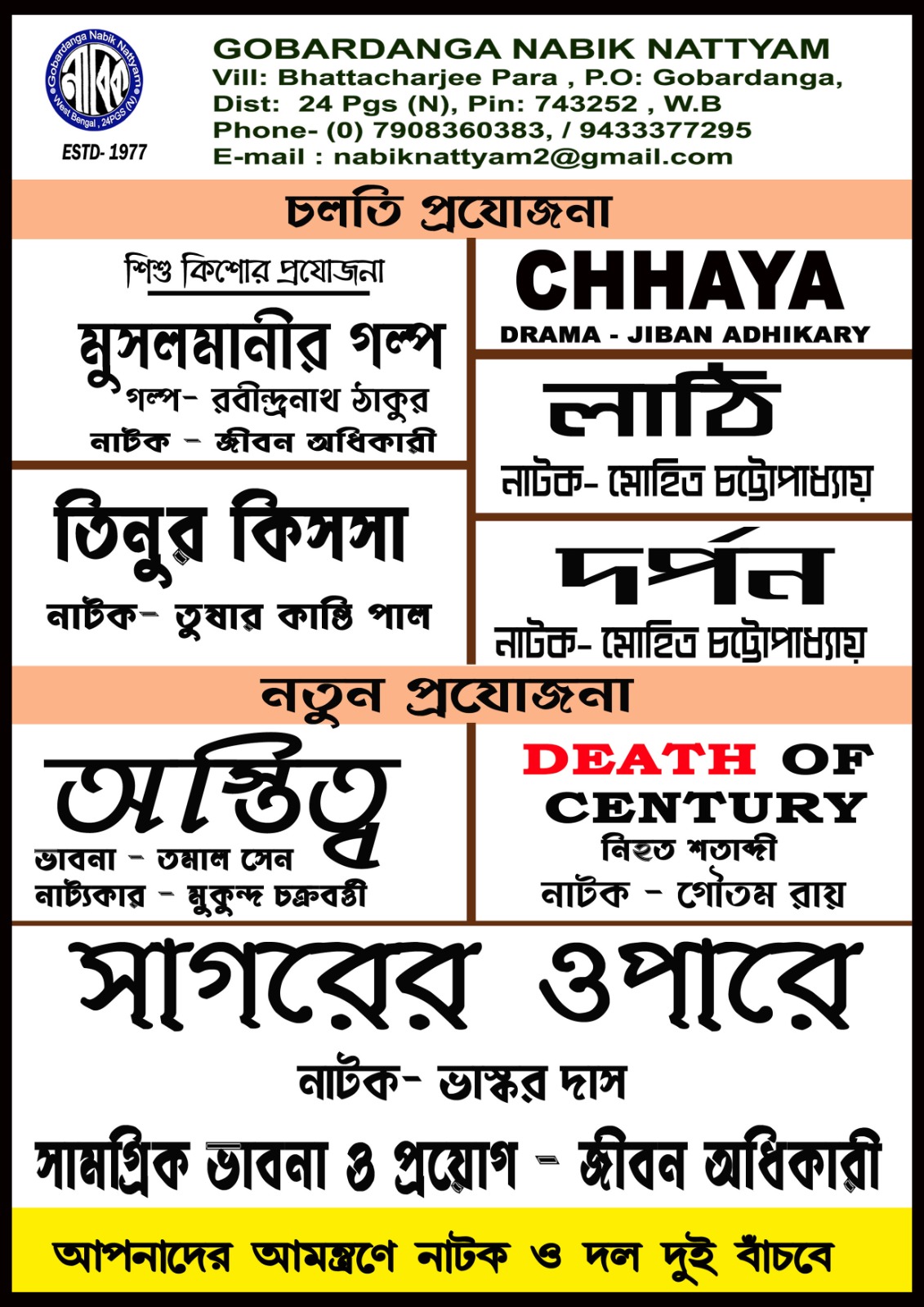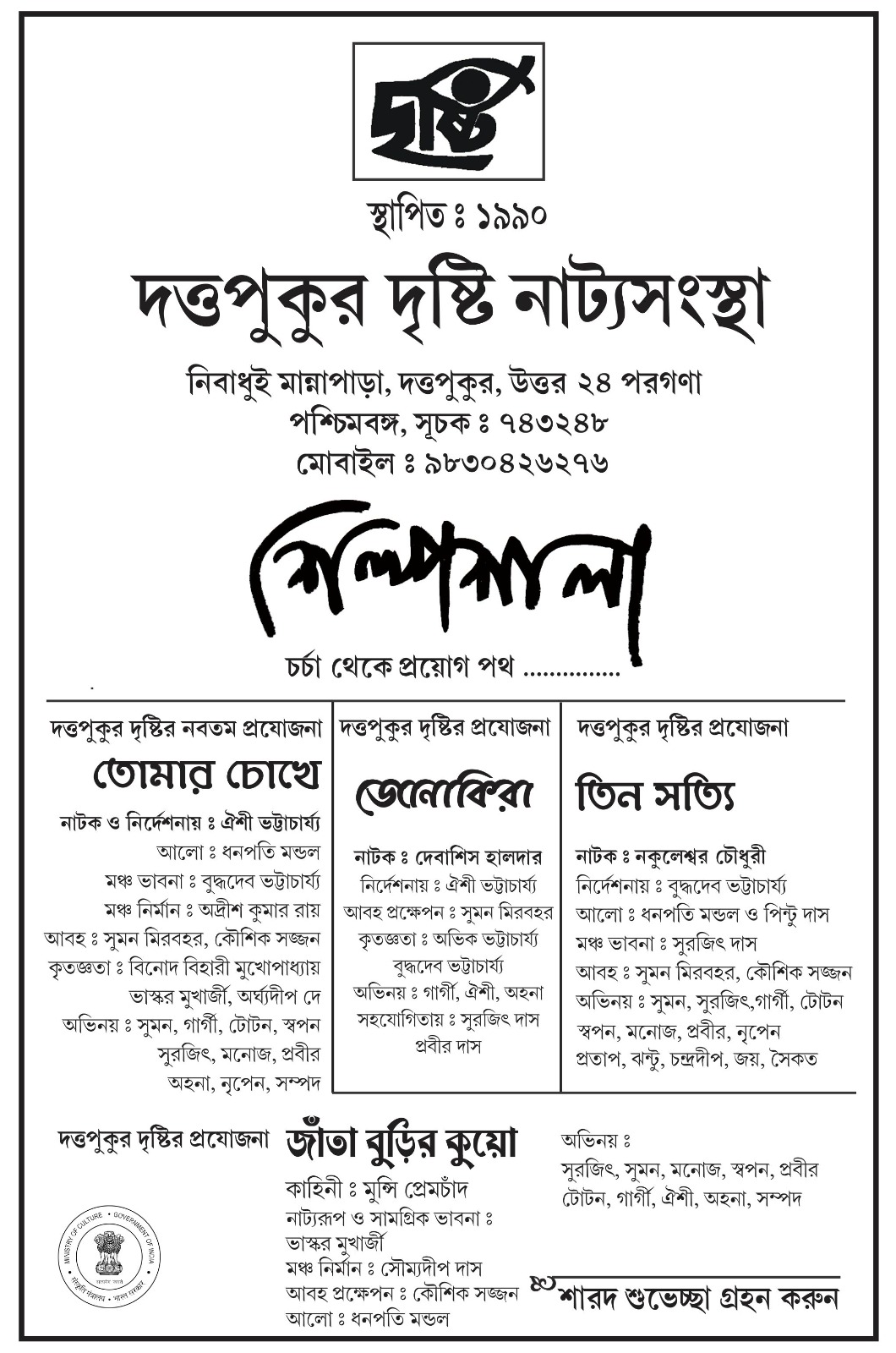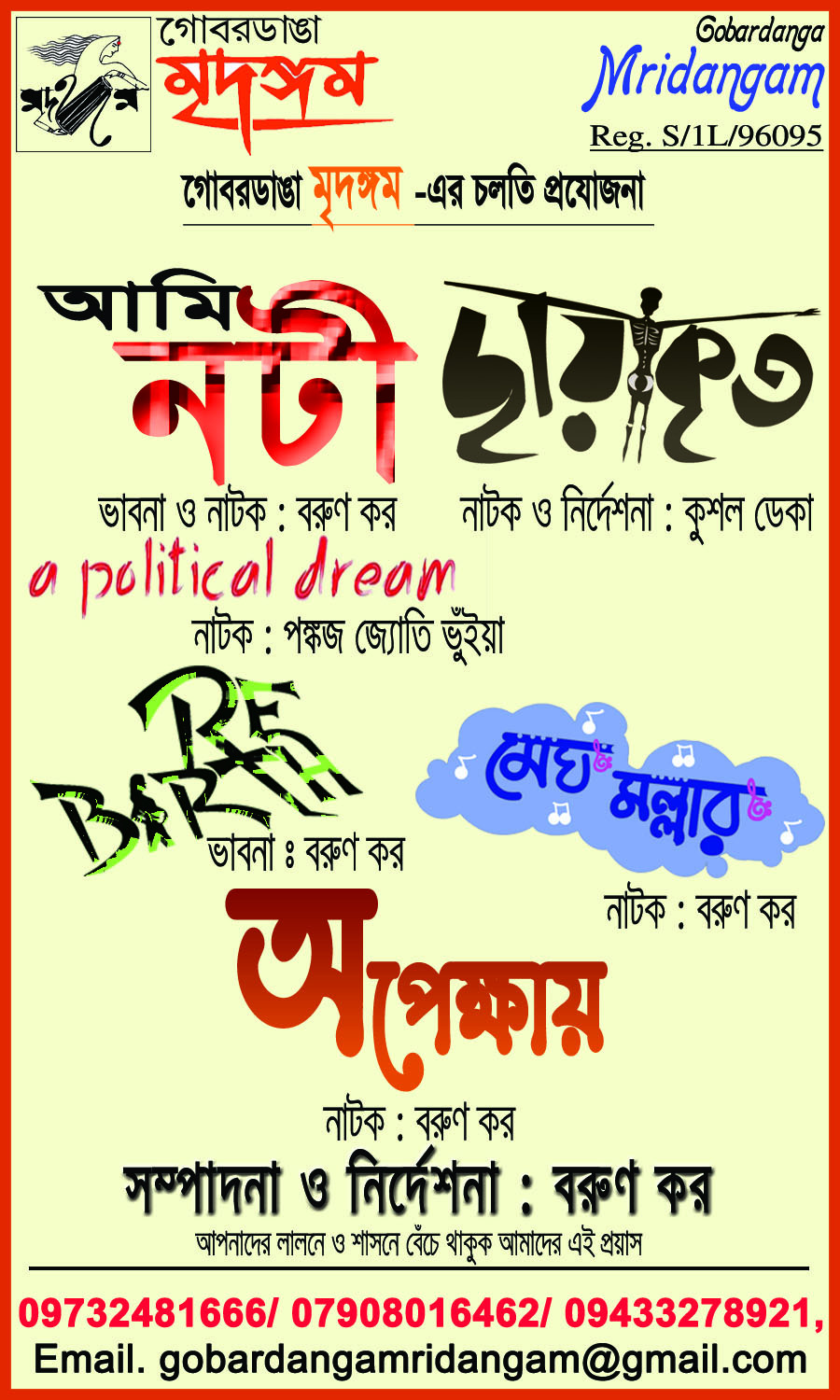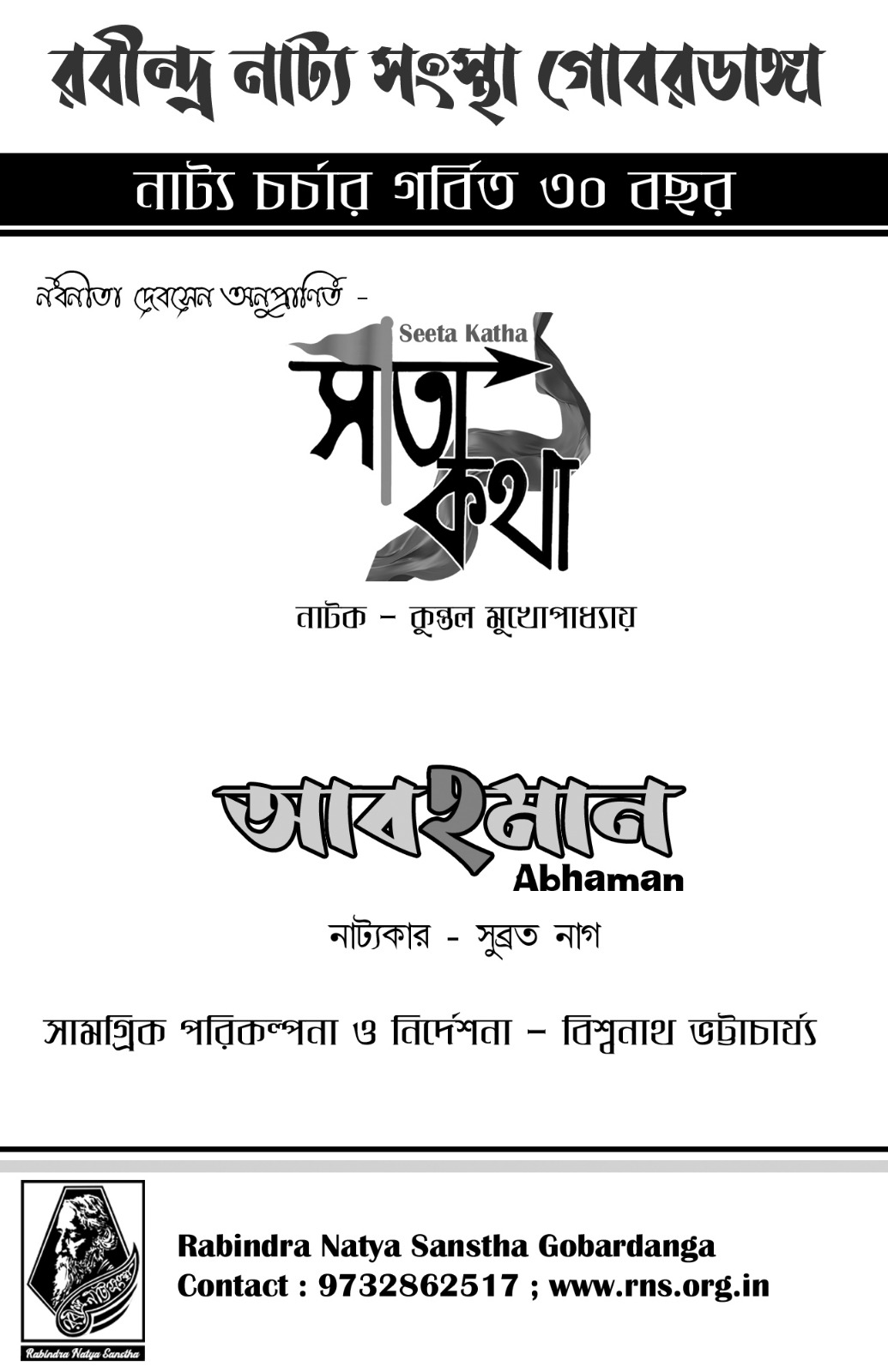শিল্পী ও তাঁর শিল্পকর্ম – প্রফেসর বাসুদেব মণ্ডল

পারফেক্ট টাইম ওয়েব ডেস্ক : মানুষের সৃজনশীল সত্তার এক স্বাভাবিক ও সহজাত প্রকৃতি হল আনন্দের উৎসারণ। সৃষ্টিশীলতাকে উপলব্ধি করার প্রক্রিয়ায় আনন্দই শিল্পীর সর্বোচ্চ অভিজ্ঞান, তার অন্তর্গত চেতনার এক অলঙ্ঘনীয় অংশ। আনন্দ, যেমন তার অভ্যন্তরীণ মর্মগত উপলব্ধি, তেমনি বহির্জগতে তার রূপান্তর এই উভয়েই শিল্পীর সৃষ্টির শিকড় প্রোথিত। আনন্দ কেবল একটি অনুভূতি নয়, বরং এটি একধরনের আধ্যাত্মিক স্তর, যা শিল্পীর সৃষ্টিকর্মের গভীরতা ও ব্যাপ্তিকে নির্দেশ করে। আনন্দের মর্মার্থ শিল্পীর কাছে বহুমাত্রিক। এটি একদিকে তার সৃষ্টিশীলতার অনুপ্রেরণা, অন্যদিকে তার আত্মচেতনার মেলবন্ধন। এই আনন্দ কেবল বাহ্যিক উপভোগ নয়; বরং এটি অন্তর্গত ও অন্তর্মুখী। যখন শিল্পী সৃষ্টিশীলতায় নিমগ্ন হন, তখন তার মানসিক ও আবেগীয় প্রকৃতি আনন্দের মধ্যে এক অদৃশ্য মুক্তি খুঁজে পায়। এ একধরনের ‘অনুভবের ঐশ্বর্য,’ যা শিল্পীকে বাস্তবতার সীমানা ছাড়িয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন বাস্তবতার দিকে নিয়ে যায়। এই অনুভূতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে গভীর আত্মানুসন্ধান। শিল্পী যখন কোনো সৃষ্টিকর্ম রচনা করেন, তখন সেই রচনার মধ্যে তার ব্যক্তিগত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং কল্পনার সমন্বয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “আনন্দই জীবনের অন্তরতম সত্য।” এই উক্তি শিল্পীর সৃজনশীলতাকে আনন্দের সঙ্গে যুক্ত করে। শিল্পী তার সৃষ্টির মাধ্যমে যে আনন্দ প্রকাশ করেন, তা একদিকে ব্যক্তিগত, অন্যদিকে সর্বজনীন। এটি শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে এক সংযোগ স্থাপন করে। শিল্পীর আনন্দের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে দর্শনের নানা প্রবণতা। আনন্দ, এক অর্থে, শিল্পীর জীবনদর্শনের প্রকাশ। প্লেটো থেকে শুরু করে হেগেল, নীটশে কিংবা ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে আনন্দের বিভিন্ন মাত্রা আলোচিত হয়েছে। প্লেটোর মতে, “আনন্দ হল আত্মার সুষম অবস্থা।” এটি শিল্পীর কাছে এক অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা ও ভারসাম্যের প্রতীক। অন্যদিকে, ভারতীয় দর্শনে আনন্দকে সৃষ্টির মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে, “আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।” অর্থাৎ, আনন্দ থেকেই সৃষ্টির উৎপত্তি। এই প্রাচীন তত্ত্ব শিল্পীর সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। শিল্পী যখন আনন্দ অনুভব করেন, তখন সেই আনন্দ কেবল অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি তার সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে জগৎকে আলোকিত করে। এই আনন্দ কখনো আবেগপ্রবণ, কখনো বৌদ্ধিক, আবার কখনো আধ্যাত্মিক। হেগেল তার ‘Phenomenology of Spirit’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, “শিল্পী কেবল তার অন্তর্গত অনুভূতিকে প্রকাশ করেন না, তিনি সেই অনুভূতিকে এমন এক স্তরে নিয়ে যান যেখানে দর্শকও সেই অনুভূতির অংশীদার হতে পারেন।” হেগেলের এই তত্ত্ব আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতার সংযোগকে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে। শিল্পীর সৃষ্টিকর্মে আনন্দ এক অনন্য ও বহুমাত্রিক রূপ ধারণ করে। একটি চিত্রকর্মে, একটি কবিতায়, একটি সুরের মূর্ছনায়—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আনন্দ নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়। একটি চিত্রকর্মে আনন্দ কখনো রঙের ব্যবহার, কখনো বা রেখার গতিশীলতায় প্রকাশ পায়। আবার, একটি কবিতায় আনন্দ শব্দের বিন্যাস ও ভাবের গভীরতায় মূর্ত হয়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আনন্দ এক আলাদা মাত্রা পায়। একটি সুরের মধ্যে যে আবেগপ্রবণতা, তা শিল্পীর অভ্যন্তরীণ আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। সুরকার যখন কোনো নতুন সুর সৃষ্টি করেন, তখন সেই সুরের প্রতিটি নোটে তার আনন্দের ছোঁয়া পাওয়া যায়। এই আনন্দ আবার শ্রোতার অনুভূতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। শ্রোতা যখন সেই সুর শোনেন, তখন তারও একধরনের অভ্যন্তরীণ আনন্দ অনুভূত হয়। এইভাবেই, শিল্পীর আনন্দ সর্বজনীন হয়ে ওঠে। আনন্দ ও শিল্পীর সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুযায়ী, সৃষ্টিশীলতা হলো অবচেতনের প্রকাশ। আনন্দ এই অবচেতনের অভিজ্ঞতাকে সজাগ করে। একজন শিল্পী তার অবচেতন মন থেকে যে অনুভূতিগুলি প্রকাশ করেন, সেই অনুভূতিগুলি আনন্দের দ্বারা চালিত হয়। আবার, কার্ল ইউনগের মতে, সৃষ্টিশীলতা হলো মানসিক চেতনার বিভিন্ন স্তরের সংযোগ। এই সংযোগ আনন্দের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়। ইউনগের ‘Collective Unconscious’ তত্ত্ব অনুসারে, আনন্দ কেবল ব্যক্তিগত নয়, এটি সমষ্টিগত চেতনার অংশ। যদিও আনন্দ শিল্পীর সৃষ্টিশীলতার প্রধান চালিকা শক্তি, তবে এই আনন্দ সর্বদা ইতিবাচক নয়। আনন্দের গভীরতার সঙ্গে দুঃখ ও যন্ত্রণার একটি সূক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে। অনেক সময়, শিল্পী তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আনন্দ খুঁজে পান। এই দ্বৈততা শিল্পীর সৃষ্টিকর্মকে আরও গভীর ও অর্থবহ করে তোলে। টলস্টয় তার ‘What is Art?’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “শিল্পের প্রকৃত রূপ হলো আবেগের অভিজ্ঞতা।” এই অভিজ্ঞতা কখনো আনন্দময়, কখনো বা বেদনার্ত। কিন্তু এই আবেগের মধ্যে আনন্দের ভূমিকা অপরিসীম। আনন্দ শিল্পীর সৃষ্টিশীলতার একটি অন্তর্নিহিত শক্তি। এটি কেবলমাত্র শিল্পীর ব্যক্তিগত অনুভূতিকে নয়, বরং তার সৃষ্টিকর্মের সর্বজনীনতাকে নির্দেশ করে। আনন্দের এই শক্তি শিল্পীর মনের গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে তার সৃষ্টিকর্মে প্রাণসঞ্চার করে। এক অর্থে, শিল্পী ও আনন্দ একে অপরের পরিপূরক। এই আলোচনায় যে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে, তা আনন্দ ও শিল্পীর সম্পর্ককে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে সহায়ক হবে। শিল্পীর সৃষ্টির অন্তরালে থাকা এই আনন্দই মানবজীবনের গভীরতর সৌন্দর্যকে তুলে ধরে।